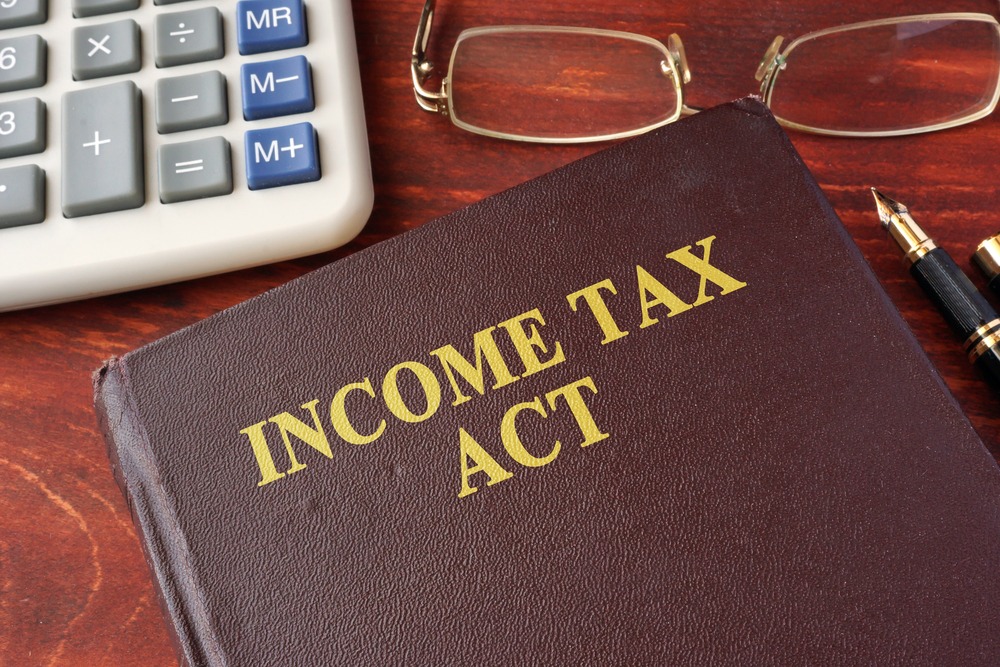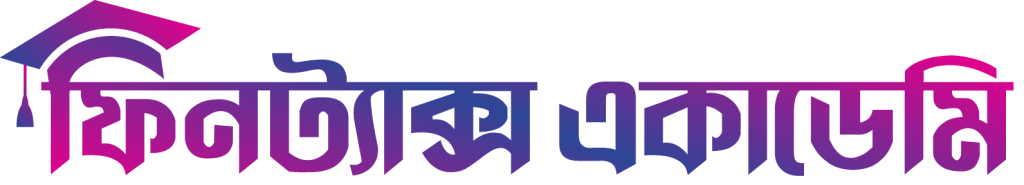বাংলাদেশে প্রগতিশীল করব্যবস্থা ব্যক্তি করদাতাদের জন্য একটি দীর্ঘস্থায়ী বাস্তবতা। এ ব্যবস্থায় উচ্চ আয়ের ব্যক্তিরা অধিক হারে কর প্রদান করেন, যা আয়বৈষম্য কমাতে একটি বৈশ্বিকভাবে স্বীকৃত এবং কার্যকরী নীতি হিসেবে কাজ করে। উন্নত বিশ্বের বিভিন্ন দেশে এ মডেল সফলতার সাথে প্রবর্তিত হয়েছে। যেখানে প্রগতিশীল করব্যবস্থা রয়েছে, সেখানে করদাতারা উন্নত স্বাস্থ্যবিমা, উন্নত মানের পরিবহনব্যবস্থা, সন্তানদের শিক্ষা এবং অবসরকালীন পেনশনসহ একাধিক সামাজিক সুরক্ষা সুবিধা ভোগ করেন।
তবে বাস্তবতায় দেখা যায়, এই কাঠামোর সবচেয়ে নিঃশব্দ ও অবহেলিত অংশীদার হচ্ছেন সেই করদাতারা, যাঁরা নিয়মিত ২৫ শতাংশ থেকে ৩০ শতাংশ হারে কর দিয়ে যাচ্ছেন। এঁদের বড় অংশই বেসরকারি খাতের ব্যবসায়ী, কর্মকর্তা ও কর্মচারীরা, যাঁদের আয়ের উৎস থেকে উৎসে কর কর্তনের (TDS) মাধ্যমে সরাসরি রাজস্ব আদায় হয়ে থাকে। তাঁদের কর ফাঁকি দেওয়ার সুযোগ নেই, নেই বিকল্প আয়ের পথ। অথচ এই নিয়মিত করদাতারা রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি বা সুবিধা থেকে প্রায় বঞ্চিত। তাঁদের জন্য নেই ওয়ান-স্টপ চিকিৎসাসেবা, নেই উন্নত মানের পরিবহনব্যবস্থা, নেই নির্দিষ্ট স্বাস্থ্যবিমা, নেই অবসরের পর সরকারি পেনশন কিংবা আর্থিক নিরাপত্তা।
ফলে করদাতাদের অবস্থান হয়ে পড়েছে একধরনের ‘রাজস্ব দাসত্ব’—যেখানে তাঁরা শুধু কর দিয়ে যান, কিন্তু রাষ্ট্রীয় কাঠামো থেকে কোনো ন্যায্য প্রত্যাশার জায়গা তৈরি হয় না। করদাতারা যেন দায়িত্ব বহন করছেন, অথচ অধিকার থেকে বঞ্চিত। এই অসম সামাজিক চুক্তি টেকসই নয়; এটি শুধু অর্থনৈতিক নয়, বরং আস্থার স্তরেও এক গভীর সংকট তৈরি করছে। ফলে দিন শেষে প্রশ্নটা জোরালো হয়ে ওঠে, ‘আমি নিয়মিত কর দিই, কিন্তু রাষ্ট্র কি আমার পাশে আছে?’
এই প্রশ্ন এখন শুধু কৌতূহল নয়, একধরনের আর্থিক ও মানসিক চাপের প্রতিচ্ছবি। আজকের প্রেক্ষাপটে অনেক করদাতা অনুভব করছেন, তাঁরা যেন রাষ্ট্রের দায়িত্ব বইছেন, কিন্তু অধিকার পাচ্ছেন না। রাষ্ট্র যেন তাঁদের ‘দায়িত্বপ্রাপ্ত’ নাগরিক হিসেবে দেখে, কিন্তু ‘অধিকারপ্রাপ্ত’ নয়। এই ভাঙন শুধু অনুভূতির জায়গায় নয়, দীর্ঘ মেয়াদে এটি রাষ্ট্র ও নাগরিকের মধ্যকার আস্থার সম্পর্ককেই দুর্বল করে তুলছে।
২০২৫-২৬ অর্থবছরের নতুন অর্থ অর্ডিন্যান্সে করহারে পরিবর্তনের ফলে নিয়মিত করদাতাদের প্রকৃত কর বোঝা ১০–২৫% পর্যন্ত বেড়েছে। অথচ তাঁদের আয়ের প্রবৃদ্ধি শূন্যের কাছাকাছি, বেতন অপরিবর্তিত, আয় স্থবির। এর বিপরীতে জীবনযাত্রার ব্যয় আগুনছোঁয়া: বাড়িভাড়া, চিকিৎসা, শিক্ষা, নিত্যপণ্য, সবকিছুর খরচ লাগামছাড়া। নাগরিক সুবিধা অপরিবর্তিত থাকলেও খরচ বেড়েছে বহুগুণে। ফলে করদাতারা এখন এক দোদুল্যমান বাস্তবতার মুখোমুখি, তাঁরা রাজস্ব দেন, কিন্তু তার বিনিময়ে স্বস্তি নয়, বরং আরও চাপ কাঁধে নিচ্ছে।
এই চাপ সবচেয়ে দৃশ্যমান হয়েছে ২০২৫ সালের জুলাই মাসের বেতনে। ২০২৪-এর ‘নতুন বাংলাদেশ গড়ার’ প্রত্যাশার পরে দেখা গেল, এক বছর পর একজন চাকরিজীবী হাতে পাচ্ছেন আগের বছরের চেয়ে কম বেতন, কেবল অতিরিক্ত করের কারণে।
আয়কর, ভ্যাট, করপোরেট ট্যাক্স, ব্যাংকিং ও অর্থনীতি বিষয়ে পাঠকদের লেখা প্রকাশের জন্য আমন্ত্রণ জানানো হচ্ছে। পাঠক ও গবেষকগণ তাঁদের গবেষণা, বিশ্লেষণ, মতামত কিংবা তথ্যভিত্তিক লেখা পাঠাতে পারবেন নির্ধারিত ই-মেইল ঠিকানায়। ই-মেইল: fintaxbd@gmail.com
এটা একধরনের নীতিগত বৈপরীত্য। যখন দুর্নীতি হ্রাস পেয়েছে, তখন রাষ্ট্রীয় ব্যয় কমে যাওয়ার কথা ছিল। কিন্তু বাস্তবে সরকার রাজস্ব ঘাটতি পূরণের চাপ দিচ্ছে মূলত বিদ্যমান করদাতাদের ওপরই। ফলে একদিকে দেশের অর্জন, যেমন রেমিট্যান্স প্রবাহ, বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ, রপ্তানি প্রবৃদ্ধি, লোন রি-পেমেন্ট সক্ষমতা ম্লান হয়ে যাচ্ছে, আর করদাতাদের বয়ে বেড়াতে হচ্ছে অতিরিক্ত করের বোঝা।
এই করের চাপ শুধু আর্থিক নয়, মানসিকও। বেসরকারি খাতে কর্মরত অনেকেই পাচ্ছেন না মূল্যস্ফীতির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ বেতন, নেই চাকরির স্থায়িত্ব, নেই ভবিষ্যতের কোনো নিশ্চয়তা। ফলে অনেক প্রতিশ্রুতিশীল তরুণ ও মধ্যবয়সী করদাতা দেশ ছাড়ার সিদ্ধান্ত নিচ্ছেন, শুরু হচ্ছে এক ভয়াবহ মেধাপ্রবাহ হ্রাস, যা রাষ্ট্রের জন্য দীর্ঘ মেয়াদে বিপর্যয় ডেকে আনতে পারে।
রাষ্ট্র যদি করদাতাকে কেবল কর সংগ্রাহক মনে করে, তবে এই সমাজচুক্তি ভেঙে পড়বে। কর চাপিয়ে দেওয়ার বিষয় থেকে সরকার তথা এনবিআরকে বের হয়ে আসতে হবে, করের নেট এবং কর ফাঁকি বন্ধ করতে হবে।
‘রাজস্ব দাসত্ব’ থেকে ‘সম্মানভিত্তিক অর্থনীতিতে’ উত্তরণের নীতিনির্ধারকদের জন্য আমার কয়েকটি বাস্তবভিত্তিক সুপারিশ:
- সর্বনিম্ন করমুক্ত আয়সীমা ৫০০,০০০ টাকা নির্ধারণ করা।
- ব্যক্তিপর্যায়ে সর্বোচ্চ করহার ৩০% থেকে কমিয়ে ২০%-এ নামানো উচিত, যেটি আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপটে বিবেচনা করলেও বেশি গ্রহণযোগ্য ও যৌক্তিক হবে।
- যাঁরা সর্বোচ্চ কর দেন, তাঁদের জন্য চালু করা যেতে পারে: পরিবারের সদস্যদের সরকারি হাসপাতালে ওয়ান-স্টপ উন্নত মানের চিকিৎসাসেবা, কর ফেরতের আওতায় জনস্বাস্থ্য বিমা অবসরের আংশিক পেনশন স্কিম, সরকারি সম্মাননা ও বিশেষ নাগরিক মর্যাদা (বিশেষ ব্যাজ, অগ্রাধিকার সেবা ইত্যাদি)।
- ‘গর্বিত করদাতা’ স্ট্যাটাসকে শুধু ডিজিটাল ব্যাজে সীমাবদ্ধ না রেখে বাস্তব সুবিধাসম্পন্ন শ্রেণি হিসেবে প্রতিষ্ঠা করতে হবে।
- কর আদায়ের আওতা বাড়াতে হবে প্রযুক্তির সঠিক ব্যবহার, প্রণোদনা ও স্বচ্ছ নিরীক্ষার মাধ্যমে—চাপ বা ভয় নয়, উৎসাহ ও আস্থার ভিত্তিতে।
- পাশাপাশি রাষ্ট্রের ব্যয়ে সংযম ও জবাবদিহি নিশ্চিত করতে হবে, যাতে করদাতার টাকা রাষ্ট্রের বিলাসিতায় নয়, ন্যায়বিচারে ব্যবহৃত হয়।
এই পদক্ষেপগুলো বাস্তবায়ন করতে পারলে কর প্রদান হবে আরোপ নয়, গর্বের বিষয় এবং অর্থনীতি গড়ে উঠবে পারস্পরিক সম্মান ও দায়িত্ববোধের ভিত্তিতে।
নতুন বাংলাদেশ গড়ে উঠবে কেবল অবকাঠামো দিয়ে নয় বরং নাগরিক মর্যাদা ও দায়িত্ববোধের ভিত্তিতে। যদি একজন করদাতা নিজেকে শুধুই ‘দাতা’ নয়, বরং ‘গর্বিত নাগরিক’ মনে করেন, তবেই গড়ে উঠবে একটি টেকসই কর সংস্কৃতি। রাষ্ট্র শুধু কর নেবে না, সম্মানও দেবে, এই বিশ্বাস ফিরিয়ে আনতে এখনই সময়।
একটি সম্মাননীয় রাষ্ট্র গড়তে হলে করদাতার সঙ্গে গড়ে তুলতে হবে মর্যাদাসম্পন্ন সংলাপ এবং নিশ্চিত করতে হবে যৌক্তিক করহার, যে ব্যবস্থায় করদাতাদের ওপর বাড়তি বোঝা চাপিয়ে দেওয়া হয় না। অন্যথায়, করপ্রণালি হয়ে উঠবে ভয়ের প্রতীক, আস্থার নয়। সে ক্ষেত্রে কর প্রদানে উৎসাহ নয়, বরং জন্ম নেবে কর-ভীতি, আর সেই ভয়েই হারিয়ে যাবে রাষ্ট্রের ভবিষ্যৎ নির্মাতারা।
লেখক: ফয়সাল ইসলাম এফসিএ, এলএলবি